
শেরপুরে ছোটকাগজ চর্চা – ২য় পর্ব
জ্যোতি পোদ্দার
শেরপুরে ছোটকাগজ চর্চা – ২য় পর্ব
স্থানিকে পাঠক বলয় যথেষ্ট প্রসারিত নয়। আর্থ-সামাজিক কাঠামো এমন যে, নিজে ও পরিবারের আহার সংস্থানে সকাল-সন্ধ্যা গতরে পরিশ্রমের পর আর ফুসরত কই? পঠন-পাঠনের যে সংস্কৃতি যে আলোড়ন যে ঝোঁক সমাজে দেখা দেবার কথা—সেটি টাউন শেরপুর কেন বাংলাদেশের কোনো মফস্বলের ভাগ্যে জুটে নাই।
সবকিছু সর্বসুখ ঐ রাজধানী ঢাকাতে—এমন মনোভঙ্গির কারণেও, স্থানিক ন্যাতিয়ে আছে ম্যাড় ম্যাড়া হয়ে আছে। সজীবতা নেই। সনদধারী বেড়েছে বটে। স্কুল কলেজ কিণ্ডার গার্ডেন কোচিংয়ের রমারমা; বাজার আছে ক্ষুদ্র ঋণের নামে নানা কিসিমের টাকার দোকান।
তাই বলছিলাম, পঠন পাঠনের সংস্কৃতি গড়ে দেবার যে সামাজিক সাংস্কৃতিক আত্মিক আন্দোলন সেটি মফস্বলে বিস্তার ঘটেনি। রাজনৈতিক টেন্ডার বাজির সাথে পাল্লা দিয়ে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের সুচক উর্ধ্বমুখী। জ্ঞান ও জ্ঞানীর সন্মান করতে হবে বলে বইযে মুখস্ত করলেও, প্রয়োগে এসে চোরাবালিতে আটকে আছে।
কড় গুণে গুণে বলে দেবার মতো পাঠকের সংখ্যা। কাজে কাজেই ছোটকাগজের বাজার বলতে ঐ গুটি কয়েকজনের করিডোর। কাগজ বিক্রি করতে গেলে কবি ও সম্পাদকের ঘাম ঝরার সাথে সাথে আগ্রহও ঝরে পড়ে মাথা থেকে পায়ে।
তদুপরি আছে কবি ও কবিতা সম্পর্কে অবজ্ঞা-অবহেলা। হোক সে পরিবার কিংবা নাগরিক সুশীলবর্গের। দ্বিমেরু রাজনীতির কারণে সুশীলেরা হালুয়ারুটি একটু ঘুরিয়ে খাবেন, তবু তরুণ কবি ছোটকাগজ নিয়ে টু শব্দ করিবেন না।
পাঠক সমালোচকের পর্যালোচনাই যে তরুণের নতুন দিশা খুলে দিতে পারে—তেমন পাঠক কিংবা সমাজ আমরা ‘সৃজন করিতে পারি নাই’।
তিন রাস্তা মোড়ে গলা ফুলিয়ে ঘণ্টার পর ঘন্টা বক্তৃতা দিতে পারি বটে, কিন্তু কোনোভাবেই চিন্তা চর্চা করবার পাঠচক্র করবার পরিসর তৈরি করবার অবসর কারো হয়নি।
কোথাও কোনো কিছু এমনি এমনি জন্ম-বিকাশ ঘটে না, তার একটা কার্যকারণ থাকে—ফসল ঘরে তোলবার পূর্বে যেমন জমি চাষাবাদের দরকার পরে; তেমনি স্থানিকের বিকাশ সার্বিকতার উপর নির্ভর করে। সেই পরিসর আমাদের কই।
শেরপুরে ছোটকাগজ চর্চা – ২য় পর্ব
পঠন-পাঠনের সংস্কৃতি গড়ে তুলবার কোনো সামিজিক ফোর্স নাই। ছাত্র শিক্ষক অভিভাবকের এখন ‘এ প্লাস’কেই মেনেছে জীবনের সার। স্কুল কলেজ শ্রেণিকক্ষ এখন স্রেফ পরীক্ষা হলো কোচিংই হলো মৌল বিদ্যাপীঠ—ভেতরে শিক্ষার্থী কোচিংয়ের বাইরে কী ভীষণ কাতরতা নিয়ে এখানে ওখানে হত্যে দিয়ে বসে আছে কালের বাবা-মা।
স্কুল-কলেজের পাঠাগার দেখেছেন? গাদাগাদা বইয়ে ঠাসা তার উপর ধুলার পরে ধুলার প্রলেপ। শিক্ষক ব্যাচের পর ব্যাচ টিউশন করিয়ে করিয়ে ক্লান্ত, মুখে আর কোনো রা বেরুই না। সব ক্যালরি শেষ। শিক্ষক রুমে বসে পান চিবাতে চিবাতে একটু ঘুমিয়ে ফুয়েল ভরে নিচ্ছে মাত্র।
এ চিত্র সর্বত্র। হোক সে শহর বন্দর জেলা কিংবা থানা শহর ইউনিয়ন পর্যন্ত এই চলচ্চিত্র কম-বেশি দেখা দেবে। গ্রাম তো সেই গ্রাম নেই। পাকা রাস্তা। ম্যাইক্রো ক্রেডিট বাংলা। গ্রামীণ আশা ব্র্যাক আপার এ-বাড়ি ও-বাড়ি উঠান বৈঠকে টাকা বেচাকেনায় ব্যস্ত।
তাই বলে স্কুল-কলেজে বার্ষিকী একবারেই হয়নি তা কিন্তু নয়। তবে তা হাতে গোনা। স্কুল-কলেজের দেয়ালিকা ম্যাগাজিন সাহিত্যচর্চার আঁতুর ঘর। সেই চর্চা স্বাধীন বাংলাদেশে বাড়েনি।
দেখভাল করার লোক থাকলেও, এই সহশিক্ষা কার্যক্রমের প্রতি একধরনের অবজ্ঞা প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে মনের গভীরে জারি রয়েছে। তবু যে ক’টি এই স্থানিকে পেলাম—বার্ষিকী/৯০, প্রপর্ণ (১৯৯০, ১৯৯৯), উৎস (২০০২), ধারা খরতর (২০১৫), কিশোলয় (১৯৯৮), শুভ্র ভোরের পুষ্পকথা (২০০৭), রজত (২০১৬), ভিক্টোরিয়া (২০১৭) ইত্যাদি।
শিশুদের জন্য কোনো বিনোদনকেন্দ্র নেই। সজীব ফসল ঘরে উঠছে। হোক সে হাইব্রিড। উঠছে পাকা দালান। টাইলস করা হাই-কমোড রো-কমোড বাথরুম। সবই হাল ফ্যাশনের। হোন্ডা চালিয়ে তরুণ শহর যাচ্ছে আড্ডা মারতে নয়তো রাস্তার মোড়ে মাথা গুঁজে নেটে ঘুরছে জগৎ সংসার। এই আমাদের প্রান্তিক জনপদের সাধারণ দৃশ্যবালি।
স্থানিকে ছোটকাগজ বের করবার প্রবণতা পড়তির দিকে। স্থানিক পাঠককে না-পেয়ে কবি-সম্পাদক এখন সিটিজেন ছেড়ে নেটিজেনে। লাইক কমেন্টসের সংখ্যায় গুনে নিচ্ছে কবিতা পড়ার রেটিং। নিউ ফিড আর টাইম লাইনেই স্থানিক কবির রমরমা বাজার।
এই উত্তর জনপদে বেড়ে ওঠা আমাদের ভূমিজরা প্রান্তিকের প্রান্তিক। গারো জনগোষ্ঠী নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে স্মরণিকা বা ভাঁজপত্র প্রকাশ করছে।
শেরপুরে ছোটকাগজ চর্চা – ২য় পর্ব
সেখানেও কবিতাচর্চার পরিসর গড়ে ওঠছে। মিঠুন রাকসাম এ অঞ্চলে বেড়ে ওঠা তরুণ কবি। তাঁর কবিতায় উঠে আসছে গারো যাপনচিত্র। দ্বন্দ্ব ও সংঘাত। আপোস ও নির্মম বাস্তবতা। মিঠুনের কবিতায় গারো কথা বলছে। গারোর কথা গারোর কলমেই উঠে আসবে—যে জীবন আমার না সে জীবনের কথা কী করে আমি বয়ান করব? সেই জীবনের জন্য দরকার হয় প্রাঞ্জল সাংমা কিংবা একজন মিঠুন রাকসাম। মিঠুনের গারো কবিতা উচ্চকিত কবিতা।
‘বৃদ্ধ নানীর সাথে মন খুলে কথা বলতে পারি না।
নানী বাংলা জানে কম
আমি মান্দি জানি কম
মুখোমুখি বসে থাকি—বোবা হয়ে যাই।
শালার নিজের ভাষাটাও ভুলে গেলাম।’
(গন্ধচোর : মিঠুন রাকসাম)
থকবিরিম—গারো সাহিত্যের কাগজ। প্রান্তিক জনগোষ্ঠী গারোদের আচিক ভাষা ও সংস্কৃতির বয়ানের কাগজ। মিঠুন রাকমামের প্রযত্নে প্রকাশিত। না, এই প্রকাশনার স্থানিক নয়—ঢাকাতে। হয়তো মিঠুনরা বুঝেছে বাঙালির তাপ চাপ ভাপের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হলে বাঙালি রাজধানীতে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রান্তিকের প্রান্তিক লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। নিজের ভাষা-সংস্কৃতিকে বাঁচার লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।
‘থকবিরিম’ মানে বাংলা ভাষান্তরে ‘বর্ণমালা’। থকবিরিম একটি প্রকাশনী সংস্থাও বটে। উদ্দেশ্য ‘গারো ভাষার সাহিত্য, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, গারো লোককথা প্রকাশের মাধ্যমে নিজ ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সাথে পরিচিতকরণ।’
গারো আমাদের পড়শী। এ ভূখণ্ড নির্মাণের কারিগর। বহু রৈখিকতার মেলাবন্ধন অনাদিকালের। দেখাদেখি চাষ লাগালাগি বাসের পড়শী গারো হাজং কোচ বানাই ডালু হদি হিন্দু মুসলিমদের যৌথ যাপনের ভুমিখণ্ড এই উত্তরের জনপদ।
লাগালাগি পাশাপাশি হাত দুরত্বের পড়শী সম্পর্কে জানাশোনা কম। যতটুকু জানাজানি দাপটের জানাজানি। নিজেকে কেন্দ্রে রেখে পরিধিকে জানাজানির মতো। কখনো কালো নেটিভ, জংলি, জমিদারবাবুর এস্টেস্টের বেগার খাটা লোক। অচ্ছুত মান্দি।
কখনো নিজের সাধর্মের শ্রেষ্ঠতার নিরিখে, কখনো ভাষাভাষীর জাতীয়তাবাদের পাটিগণিতের সুদকষার হিসাব সূত্রে মন্দার্থে জানাজানি; নীচুতার নিক্তির মাপমাপি। বাঙালি হবার প্ররোচনায়—এক রৈখিক রেখার পাঠ। অথবা জাতিসত্ত্বার অস্তিত্ব অস্বীকার করার রাজনৈতিক পাঠ।
শেরপুরে ছোটকাগজ চর্চা – ২য় পর্ব
কিন্তু কখনো গারো জনগোষ্ঠীর নিজস্বতার নিরিখে যাপনের রসায়ন দিয়ে বুঝতে চাইনি। খুব বেশি গারো কাগজ সংগ্রহ করতে পারিনি। পড়শীর সাথে আমারও কম দূরত্ব নয়। রবেতা ম্রং কিংবা সুদীন চিরান, অথবা প্রাঞ্জল এম সাংমা আমার একমাত্র জানালা—ছোট্ট জানলা। সেখান থেকে সংগৃহীত—ব্রিংনি বিবাল(২০০৯), ওয়ানগালা (১৯৯৯), আসপান (২০১৫) ইত্যাদি প্রপাত্ত রেখেছি পাঠকের জন্য।
ঋদ্ধ হোক থকবিরিম। থকবিরিম নিজস্বতার বিকাশে গেয়ে উঠুক নিজের গান সে বলুক—সকলের সাথে আমার অবারিত যোগ আছে। বৈচিত্র্যই সুন্দর। ক্ষুদ্রই সুন্দর। সংখ্যাধিক্যের খাড়াখাড়ি দাপট নয়; গড়ে উঠুক মানুষের আড়াআড়ি বুনট। পারস্পরিক নির্ভরতার দ্যোতনা।
ব্যক্তি ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে। চর্চায় নিজে সকলকে ছাড়িয়ে যায়—যেতেও পারে—তাঁর মনোভূমি এক সার্বিকতার ছবি আঁকে। রিলিজিয়নকে একান্ত ব্যক্তিকতার কোঠরে প্রাইভেসির করিডোরে ফেলে দিয়ে মানুষকে মানুষ হিসেবে খাড়া করবার লড়াই সংগ্রাম—রাষ্ট্র ও ধর্ম কে আলাদা করে—সেকুলারপন্থীকে সংগ্রাম করতে হয়। এ সংগ্রাম রাজনৈতিক সংগ্রাম। দীর্ঘদিনের সংগ্রাম। শুধু বাচনিকতা এর বাইরের খোলসমাত্র।
কিন্তু পাশ্চাতের সমাজকাঠমোর বুনন দিয়ে তো আমার সমাজ গঠিত নয়। তার আছে নিজস্ব ধরনধারণ। ব্যক্তি ধর্মনিরপেক্ষতা চর্চা করলে বটে, কিন্তু আমাদের পরিবার সমাজ ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চা করেনি।
বারো মাসে তেরো পার্বনের রিচুয়াল নিয়েই তার দিনগুজরান করতে হয়—দীর্ঘদিনের সংস্কার অভ্যাস রিলিজিয়ন ভিত্তিক অনুষ্ঠানে তাকে যুক্ত হতে হয়—সমাজের স্বভাব আর প্রভাব দুম করে উঠে যায় না; যেতে পারে না—তার জন্য যে রাজনৈতিক সংগ্রাম সেটি আমরা করে তুলতে পারিনি। এই সংগ্রাম হয়ে ওঠা সংগ্রাম। পুরনো খোলস থেকে বের হয়ে নতুনত্বের স্বাদ গ্রহণ—সেটি খস করে কাগজে লিখলেই পরিবর্তন হবার নয়।
তার জন্য যে রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা তার অভিমুখ এখন বীজাকারে বীজেস্থিত। আমরা প্রত্যাশা করতেই পারি কোনো আগামী ভবিষ্যৎ।
শেরপুরে ছোটকাগজ চর্চা – ২য় পর্ব
—যা বলছিলাম। ধার্মিক আয়োজিত অনুষ্ঠান স্যুভিনিয়র বা কোনো স্মরণিকা বের করা নতুন নয়। এটি কখনো গুরুত্বের সাথে দেখা হয়নি। পত্রিকা প্রকাশ রিচুয়ালের কোনো অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়, বরং তরুণ যে উৎসবে মেতে উঠে পুজা সংখ্যা বাহারি উৎসবের গায়ে একটি পালক যুক্ত করার ভেতর দিয়ে উৎসবকে আরেকটু রঙিন করে তোলে, পাশাপাশি মহল্লার তরুণ লিখিয়ে হাত মকশো করার একটা পরিসর পায়। কে জানে হয়তো এই কাগজটিই হতে পারে তরুণের উস্কে দেয়া কাঠি—জ্বলে ওঠতে পারে মুহূর্তে অন্ধকার ভেদ করে।
টাউন শেরপুরে একটা সময় এই চর্চা ছিল। শারদীয়া (১৯৯২), আদ্যা (২০১৪), স্মরণিকা (১৩৯২), দশভুজা (১৯৮৬), অঞ্জলি (১৪১৯), শারদ অর্ঘ্য (১৯৮৭) অন্যত্র দেখিনি। উৎসব উদযাপন পরিষদ এমন উদ্যোগকে স্বাগত জানানো উচিত।
স্মরণিকার চাতালে যে শুধু সাহিত্যচর্চা হতে পারে তা কিন্তু নয়—ধর্ম সংক্রান্ত আলোচনাও হতে পারে; হতে পারে পড়শী সংখ্যা গরিষ্ঠ কোনো মানুষ লেখাপত্র। এতে করে সমাজে মানুষে মানুষে আরো একটি ব্রিজিং সৃষ্টি হতে পারে।
শুধু মুখে বকবক করলে ‘সম্প্রীতি’ বজায় থাকে না, নিজের উঠানে অপরকে স্পেস দেবার মনোভঙ্গিও থাকতে হয়, আর তখনই ‘ধর্ম যার যার উৎসব সবার’—কথাটির কার্যক্ষমতা দ্যোতিত হয়। এটি শুধু সনাতনীদের একার চর্চার বিষয় না—দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের চর্চার জমিনও বটে।
স্থানিকে উৎসব স্মরণিকা তেমন একটা চাতাল হতে পারে। পুজাসংখ্যা কালেভদ্রে বের হলেও, স্থানিকে ঈদ সংখ্যা কড়ে আঙুলে গোনার মতো অবস্থা। আটের দশকে দুরন্ত চৌধুরী কয়েকবার ঈদুল আজহা সংখ্যা করেছিলেন। বিভিন্ন নামে করলেও ‘আলোড়ন’ নামেই একাধিকবার করেছেন। নয়ের দশকে সুহৃদ জাহাঙ্গীর ‘ঈদ সংখ্যা’ নামে তাঁর নিযমিত কাগজ ‘আড্ডা’র একবার শুধু নামাঙ্কন করেছিলেন।
‘আলোড়নে’ ধর্ম ধর্মাচারের নানা বিধিবিধান নিয়ে আলোচনা থাকলেও, ‘আড্ডা’তে শুধু ঈদ সংখ্যা লেখা—এ ছাড়া টাউন শেরপুরে এখানকার সাপ্তহিক দশকাহনীয়, চলতি খবর বা সাপ্তাহিক শেরপুর ঈদ সংখ্যা করবার উদ্যোগ দেখলেও, ইসলামিক আন্দোলনের সাথে যারা জড়িত—হোক জড়িত শরিয়তী বা মারফতি—কাউকে ঈদকে কেন্দ্র করে ধর্ম-সাহিত্যচর্চার চাতাল নির্মাণের চেষ্টা দেখিনি।
শেরপুরে ছোটকাগজ চর্চা – ২য় পর্ব
বড় বড় মিডিয়া হাউজের কথা আমি বলছি না—বলছি কোনো স্থানিকতায় পঠন-পাঠন কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়বার যে মামলা মোকদ্দমা—আমি তার কথা বলছি। স্থানিকের অনাবাদী জমিন কর্ষণ না-করলে কোনো সোনাই ফলবে না। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে আমিনের মাপা জমির কথাই শুধু বলছি না—বলছি স্থানিকে মনোভূমি কর্ষণ করার কথাও। স্থানিকতার বিনির্মান ছাড়া একটি দেশের আর্থসামাজিক কাঠামো গড়ে উঠতে পারে না।
রাজনীতির কেন্দ্রীভূত নীতি স্থানিককে করে রেখেছে ভাগাড়। তার বিকাশের কোনো পরিসর সে রাখেনি। সংবিধানের পাতা থেকে কথাগুলো বের হয়ে আর পরিধির দিকে আসার সম্ভবনাকে সে করে রেখেছে চুয়ে পড়ার উপনিবেশিক নীতি শৃঙ্খলায়।
প্রকাশ উন্মুখ তরুণের প্রথম চাতাল হচ্ছে ‘ভাঁজপত্র’। কবি যশপ্রার্থীর তরুণের রাখ রাখ ঢাক ঢাক গুড়ের ব্যবস্থাপত্রের নাম ভাঁজপত্র। চারপাতা ভাঁজের ভেতর বন্ধুদের কাঁচালেখা অথবা নিজের ছদ্মনামে একাধিক লেখা প্রকাশের মাধ্যম ভাঁজপত্র।
সহজে কম পয়সায় বের করা যেমন যাচ্ছে, তেমনি সহজে স্মৃতি থেকে হারিয়েও যাচ্ছে—এমনকি প্রকাশিত কপিটিও পাবার জো নেই। টাউন শেরপুরে ভাঁজপত্র—ইস্ক্রা (১৯৮৫), কবিতার কাগজ (১৯৮৯), ছাপ (১৯৯২), চিত্রচেতনা (১৯৮৬), সুড়ঙ্গ (২০০৮), উপমা(২০০৮), উত্তরণ (২০০৫), আর্তনাদ(২০১৭), মুহিম নগরের ট্রেন (২০১৮), দিপ্তী (২০০৩), সিঁড়ি (২০১১), শুভেচ্ছা (২০০৭), মুক্তি (২০১৬), পদাঙ্ক ( ২০০৬), মধুকর (২০১৯), আলোর মিনার (২০১৯), মুক্ত বিহঙ্গ (২০১১), পদ্মপাণি (২০১৮) ইত্যাদি প্রকাশিত ভাঁজপত্র।
দেয়ালিকার চল একেবারেই উঠে গেছে। শ্রেণি শিক্ষকের উদ্দীপনায় মেতে ওঠা শিক্ষার্থীদের দিবসকেন্দ্রিক তৎপরতা। সুন্দর হাতের লেখা আর বাহারি রঙের কাজ করা দেয়ালিকা যখন স্কুলমাঠে কিংবা দেয়ালে ঝুঁলে—তা দেখার আনন্দ আজকাল শিক্ষার্থী পাচ্ছে কি? খুব কম স্কুলেই দেয়ালিকা হয়। কয়েক বছর আগে টাউন শেরপুরে ‘জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে’ উপলক্ষ আয়োজিত অনুষ্ঠানে দু’টি স্কুলের দেয়ালিকা দেখেছিলাম।
অন্যান্য ক্লাব অথবা পরিবেশবাদী সংগঠন কিংবা শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকেও বিভিন্ন প্রান্তিকে সাহিত্যচর্চার পরিসর নির্মাণে তৎপরতা লক্ষণীয়। দিবসভিত্তিক যেমন তেমনি সমাজ সংস্কৃতির প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেও গড়েছে সংগঠন। ‘অরুনোপল’ তেমনি একটি সংগঠন। এক স্ববপ্নবাজ তরুণ—রমিজুল ইসলাম লিসানের ব্রেইনচাইল্ড—অরুনোপলে। এদের মুখপাত্র সাহিত্য সংস্কৃতির সমাহার ‘উৎস্বর্গ।’
শেরপুরে ছোটকাগজ চর্চা – ২য় পর্ব
কিন্ত বেদনা এই যে, লিসানকে আমরা হারিয়েছি ব্রেইনস্ট্রোকে ২০২০ সালের ২০ জানুয়ারিতে। লিসানের ভেতর বড় এক সংগঠককে আমি দেখেছিলাম। বিকশিত হবার আগেই লিসান চলে গেল। টাউন শেরপুর একজন ভাবী নেতা হারালো।
বিভিন্ন সংগঠনভিত্তিক ছোটকাগজ হলো—আমাদের পাখি (২০১৯), রঙধনু (২০০৫), ফোঁটা (২০১৮), দেশের কথা (২০০৪), বাতিঘর (২০১৫), বিন্দু (২০০৯), উৎস্বর্গ (২০১৬), কংস (১৯৯০) ইত্যাদি নানা সংগঠনের সাহিত্যচর্চার চাতাল।
স্থানিকের কাজগুলো এক মলাটে আনার ধারণা থেকেই মূলত ১৯৭০ সাল খেকে ২০২০ পর্যন্ত প্রকাশিত ছোটকাগজের হদিশ দিয়েছি মাত্র। বাছাইয়ের কোনো বাটখারা বা নিক্তি রাখা হয়নি। প্রাপ্ত সকল ছোটকাগজের তথ্য-উপাত্ত দেবার পাশাপাশি নিজের কিছু কথাবার্তা ভরে দিয়েছি—সংযোগের মশলা হিসেবে, এর চেয়ে বেশি কিছু করি নাই।
তবে হ্যাঁ, যে সকল কবিতা উদ্ধৃতি দিয়েছি—সেগুলো আমার ব্যক্তিগত পছন্দের বাছাই, সমগ্রদেশের প্রেক্ষিতে কোনো তুলনা আমার লক্ষ ছিল না—স্রেফ স্থানিকের মনভূমির কর্ষিত জমিনকে দেখা ও দেখানোর পায়তারা; আর কী করে মনোভূমি দৈর্ঘ্যপ্রস্থ গভীরে বাড়ানো যেতে পারে ভেতরে ভেতরে গোপন এক টান সদা হাজির থেকেছে—সেটি হোক শেরপুর কিংবা নাচোল অথবা কাউখালী—টাউন শেরপুরের স্থানিকতা উপলক্ষ মাত্র।
(চলবে)
…………………
পড়ুন
কবিতা
রাংটিয়া সিরিজ : জ্যোতি পোদ্দার
প্রবন্ধ-গবেষণা
টাউন শেরপুরে প্রথম রবীন্দ্রজয়ন্তী
শেরপুরে ছোটকাগজ চর্চা – ২য় পর্ব

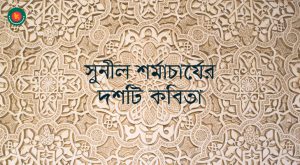
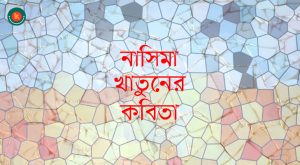
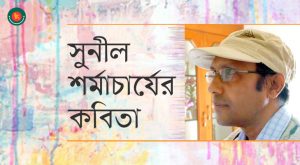
10 thoughts on “শেরপুরে ছোটকাগজ চর্চা – ২য় পর্ব”